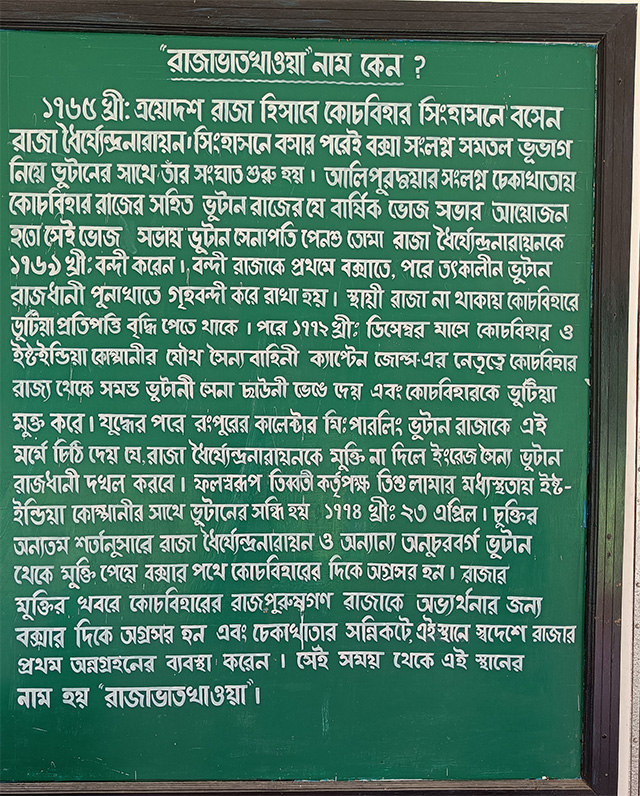নারায়ণপুর ? না কি যেন বললে ? ওটা কোথায় ? – এই ছিল বুম্বার প্রথম প্রতিক্রিয়া।
আমি বললাম – বাঁকুড়ায়। মানে ধরে নে , আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার পথ। একশো পনেরো কিলোমিটার মতো।
আরে জায়গাটার পুরো নামটা বলো , ম্যাপে দেখতে হবে তো – বুম্বা বললো।
কি আছে ওখানে ? – বুম্বা কৌতূহলী হয়ে উঠলো। বললাম – টেরাকোটা মন্দির , জমিদারবাড়ি, আর একটা জায়গায় আমি যেতে চাই , জঙ্গল পাঁচমাথা।
আমি , বুম্বা , বুম্বার সাধের মারুতি গাড়ি আর তার সাথে যদি গুগল ম্যাপ থাকে , তাহলে সে এক সাংঘাতিক কম্বিনেশন তৈরী করে। কত পথ যে আমরা ভুল করেছি , কত জায়গায় গিয়ে যে হারিয়ে গিয়েছি , সেসব অভিজ্ঞতার গল্প করলে একটা বই লেখা হয়ে যাবে। পরে কোনো পোস্টে সেসব গল্প করা যাবে। আপাতত আমরা দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললাম। কবে , কখন আর কারা যাবে নারায়ণপুর। পুরো নাম হাদাল নারায়ণপুর। এইটি যে জায়গাটার নাম সেটি আমি জানতাম। আমার ধারণা পাল্টালো যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম।
সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পৌঁছলাম শক্তিগড়। লুচি তরকারি আর বিখ্যাত ল্যাংচা সহযোগে প্রাতরাশ সেরে যখন আবার গাড়িতে চেপে বসলাম , তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে। এপ্রিল মাসের গরমে , বাইরের আবহাওয়া দেখলে মনে হবে যেন বেলা গড়িয়ে এগারোটা বেজে গেছে। তাই গাড়ির ভেতরে এসি চালাতেই হলো। এই যাত্রায় আমার সঙ্গী আমার স্ত্রী , ছেলে আর আমার বন্ধু সুব্রত। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বুম্বা। বুম্বার বাঁপাশে বুম্বার বিখ্যাত স্যামসুং ফোন , আর তাতে ছাই রঙের ওলিতেগলিতে নীল দাগের পথ দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপ।
দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে সোজা এলাম বর্ধমান , সেখান থেকে দামোদরের ব্রীজ পেরিয়ে আমরা এলাম বাঁকুড়া রোডে। ম্যাপ অনুযায়ী , বাঁকুড়ার এক জনপ্রিয় টাউন সোনামুখীর দিকে যেতে হবে। সেই পথে এগোতে লাগলাম। বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম ম্যাপ আমাদের সড়ক ছেড়ে ডানদিকের রাস্তায় যেতে বলছে।

এই উপলক্ষ্যে বুম্বার ফোনের এক বিশেষ বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করতে চাই। এটি ফোনটিকে, অন্যান্য সাধারণ তুচ্ছ ফোনেদের ভীড়ে অসাধারণ করে তোলে। ধরুন এই ফোনে ফোন এলেই তৎক্ষণাৎ রিং হতে থাকে, কিন্তু যিনি ফোন করেছেন, তাঁর নাম বা ফোন নম্বর দেখা যায় মিনিটখানেক পরে। আবার ধরা যাক , আপনি ফোনটিতে গুগল ম্যাপ চালিয়ে যাচ্ছেন , আপনার সামনে দুটো রাস্তা রয়েছে। ফোন আপনাকে ডানদিকে যেতে বলছে , আপনি ডানদিকের রাস্তা ধরে এক কিলোমিটার চলে গেলেন। তারপর হঠাৎ ফোন আপনাকে বলে বসলো যে নাহ বামদিকে যেতে হতো। আবার ইউ টার্ন নিয়ে যেতে হলো বামদিকে। এটি হলো ফোনটির ধীর স্থির ব্যক্তিত্বের একটি দিকমাত্র। উনি , সবদিক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন , যেমন ধরুন ইন্টারনেট আছে কিনা , ম্যাপ আপডেট হয়েছে নাকি ইত্যাদি। মুশকিল হচ্ছে , এই বিচার বিবেচনা করে পথ দেখাতে ওনার একটু সময় লাগে। কখন পনেরো মিনিট , আবার কখনো আধ ঘন্টা। আমরাই গাড়ি চালাতে গিয়ে ওনাকে অযথা তাড়া দিই।
এবারো তার অন্যথা হলো না। ডানদিকের রাস্তা ধরে আমরা পৌঁছলাম ধগড়িয়া স্টেশন। এবার আমি ফোন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে খুঁজতে লাগলাম যদি কোনো মানুষের দেখা পাওয়া যায়। ঘড়িতে বেলা এগারোটা। খাঁ খাঁ রোদে চারিদিক জনমানবহীন। কিন্তু প্রকৃতি এখানে বেশ উদার। অনবরত বসন্তের মৃদু বাতাস বয়ে চলেছে , যা এই আবহাওয়াতেও আরামদায়ক। বাংলার গ্রামে গ্রামে যখনি গেছি , এরম রূপেই প্রকৃতিকে আমি দেখেছি। কিছুদূর থেকে একজন লোককে সাইকেলে চেপে আসতে দেখলাম। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম – দাদা, নারায়ণপুর যাবো , কোন রাস্তা ধরতে হবে ?
উনি বললেন – ও , হদল নারায়ণপুর ? আমি বললাম – হ্যাঁ।
তা এই রাস্তায় কেন ? আরেকটু পিছনে গিয়েই তো ভালো রাস্তা ছিল। এতো এগিয়ে এসেছেন।
দূরে রেলগেটের দিকে ইশারা করে বললেন – ওই যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে , ওই রাস্তা ধরেও যেতে পারেন পাঁচ কিলোমিটারের পথ।
ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আবার গাড়িতে চাপলাম। জায়গাটার নামের উচ্চারণ এবার আমার কাছে পরিষ্কার হলো। হদল নারায়ণপুর। একযোগে সব্বাইকে জানিয়ে দিলাম। এরপর ভদ্রলোকের কথামতো এগিয়ে চললাম। বুম্বার ফোনকে কিছুক্ষণ রেস্ট দেয়া হলো। অনেকটা পরিশ্রম গেছে তো ! উনি একটু বিশ্রাম নিক।

কিলোমিটার খানেক চলার পর পৌঁছে গেলাম নারায়ণপুর। নারায়ণপুর জায়গাটা বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের অন্তর্গত। নারায়ণপুরের যেই জায়গায় এসে আমরা পৌঁছলাম , সেই জায়গাতেই রয়েছে ব্রহ্মাণী মন্দির। মন্দিরের সামনেটায় রয়েছে নাটমন্দিরের মতো নির্মিত একটি মণ্ডপ। মণ্ডপের চালে টিন ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্যিক গঠনশৈলী বাংলার অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরের থেকে আলাদা। মণ্ডপ পেরিয়ে মন্দিরের মূল গর্ভগৃহ। ব্রহ্মাণী মায়ের মূর্তির গঠন অবাক করার মতো। কষ্টি পাথরের তৈরি এই মূর্তি যে কতটা প্ৰাচীন তার সঠিক ধারণা আমার নেই । অন্ধকারে পুরোপুরি বোঝা না গেলেও, দেবীর চারহাত এবং একটি হাতে ত্রিশূল লক্ষ্য করা যায় । অনেকের মতে এটি দেবী পার্বতীর মূর্তি। স্বপ্নাদেশ পেয়ে মূর্তি স্থাপনের কাহিনী জনমুখে প্রচলিত। তবে স্থানীয় লোকেদের কাছে এই মন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে মায়ের মূর্তির গঠনশৈলী আমাকে অবাক করলো । মূর্তির বয়স কম করে হলেও হাজার বছর হতে পারে। এ ধরণের মূর্তি পাল ও সেনযুগের বিভিন্ন মন্দিরের ছবিতে দেখেছি। ব্রহ্মাণী মন্দিরের গঠনশৈলী সাদামাঠা , প্রাচীন মন্দির বলতে আমরা যা বুঝি , এ মন্দিরে সেটি দেখতে পেলাম না।

এই সময় দেখা হলো গ্রামের এক যুবক বিকাশবাবুর সাথে। তাঁর সাথে কথা বলে এই গ্রাম সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। যেমন হদল আর নারায়ণপুর দুটো আলাদা জনপদ। নারায়ণপুরের পোস্ট অফিস হদল। দুই জনপদের মাঝে রয়েছে বোদাই নদী। উনি আরো জানালেন , যে নদী পেরিয়ে আমরা এখানে এসেছি, সেটি শালী নদী। জানতে পারলাম, নারায়ণপুরের জমিদার বাড়ি তিনটি তরফে বিভক্ত। ছোট, বড় এবং মেজো। তিন তরফেই দেবী মহামায়ার আরাধনা করা হয়, আবার তিন তরফেই কুলদেবতা দামোদর মন্দির রয়েছে। জমিদার পরিবার মন্ডল উপাধি প্রাপ্ত। কৌতূহলের বসে জিজ্ঞেস করলাম , এখানে কোনো জঙ্গল পাঁচমাথা বলে জায়গা আছে নাকি ? উনি জানালেন – ওনার জানা নেই। এরম কোনো নাম উনি শোনেননি। একটু হতাশ হলাম।

এরপর সবাই মিলে হেঁটে এগিয়ে চললাম এখানকার জমিদার মন্ডল পরিবারের তৈরী পুরাকীর্তি গুলিকে প্রত্যক্ষ্য করতে। ইতিহাসবিদদের মতে জনৈক মুচিরাম ঘোষ মল্ল রাজাদের আমলে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। নিজের কৃতিত্বে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তার কাজের পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং মন্ডল উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাদের পরিবারের তরফ থেকে তৈরী হয় এই পুরাকীর্তিগুলো । আমাদের যাওয়ার পথে সবার প্রথমে দেখতে পেলাম ছোট তরফের বাড়ির প্রকান্ড প্রবেশ দ্বার ।

প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যায় সুবিশাল নাটমন্দির । বাড়ির প্রাঙ্গনেই তিনশো বছর পুরোনো রাধা দামোদর মন্দির অবস্থিত । ছোট তরফের এই মন্দির টেরাকোটা সজ্জিত। টেরাকোটা অলংকরণের কাজ দেখার মতো। নবরত্ন শৈলীর এই মন্দিরের ভিত্তিবেদী অনেকটাই উঁচু। সম্প্রতি মন্দিরের সংস্কার হয়েছে, নতুন করে রং করা হয়েছে । মন্দিরের টেরাকোটার কাজে মৃত্যুলতা ও অন্যান্য মূর্তি দেখতে অসাধারণ লাগছিলো। তবে যে কাজটা আমার নজর কাড়লো, সেটা হলো ত্রিখিলানের উপরে মাঝের দিকে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের চিত্রায়ন। কি নিপুণ কাজ !!

ছোট তরফ থেকে সোজা রাস্তা ধরে গেলে পৌঁছনো যায় বড়ো তরফে। তার আগেই রাস্তার ডানদিকে চোখে পড়লো আরো কিছু পুরোনো মন্দির। মন্দিরগুলির অনেকটাই ধ্বংসাবশেষে রূপান্তরিত। তবুও একটা পঞ্চরত্ন মন্দিরে টেরাকোটার কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। সেই টেরাকোটার কাজে রাম রাবনের যুদ্ধ , অনন্তশায়ী বিষ্ণুর চিত্রায়ন দেখার মতো।

এগিয়ে গেলাম বড়ো তরফের দিকে। বড়ো তরফে প্রবেশ করতে প্রথমেই চোখে পড়লো এক বিশাল রাসমঞ্চ। ১৭ চূড়াবিশিষ্ট , অষ্টকোণ এই রাসমঞ্চের স্থাপনকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা মুশকিল । তবে এটিও যে প্রাচীন পুরাকীর্তির মধ্যে পড়ে , এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এরম রাসমঞ্চ বাংলার ইতিহাসে বিরল।

রাসমঞ্চের পাশেই মূল জমিদার বাড়ি। ইতিহাসবিদদের মতে এই অট্টালিকার গঠনশৈলীতে একটি ইউরোপীয় ছাপ রয়েছে। জানালা গুলির ওপরে বানানো মুখগুলি , একটি সিংহের মূর্তি এইগুলো প্রত্যক্ষ করার অনুভুতিই আলাদা। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে চোখে পড়ে দুর্গাদালান এবং তার সামনের নাটমন্দির। উঁচু স্তম্ভগুলি সেকালের জমিদারবাড়ির আভিজাত্যের প্রতীকের মতো দাঁড়িয়ে।

এরপর আমাদের সাথে আলাপ হলো জমিদার বাড়ির এক সদস্য গোপাল মন্ডলের সাথে। তিনিই আমাদের বড়ো তরফের দামোদর মন্দির ঘুরিয়ে দেখালেন। বাড়ির অন্দরমহলে অবস্থিত বড়ো তরফের দামোদর মন্দির। পঞ্চরত্ন এই মন্দিরের স্থাপনকালে ১৭২৮ শকাব্দ। ত্রিখিলান বিশিষ্ট এই মন্দিরের দেয়ালে টেরাকোটার কাজ দেখা যায়।


মন্ডলবাবুর থেকে দিকনির্দেশ নিয়ে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম মেজো তরফের দামোদর মন্দির দেখতে। বাকি দুই তরফের থেকে একটু ভেতরদিকে অবস্থিত এই মন্দির। নবরত্ন শৈলীর এই মন্দির টেরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ। মন্দিরের এই দেয়ালেও রাম রাবনের যুদ্ধ আর অনন্তশায়ী বিষ্ণুর চিত্রায়ন বিদ্যমান। এরপর মন্ডলবাবুর থেকে বিদায় নিয়ে দামোদর ক্যানাল এর দিকে চললাম।

আশেপাশের কিছু পথচলতি মানুষের থেকে জানতে পারলাম , নারায়ণপুর থেকে ৩-৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দামোদর ক্যানাল লাগোয়া সেতু , যার অন্য পারে রণডিহা ব্যারেজ আছে । রণডিহা ব্যারেজ থেকে খুব কাছেই অবস্থিত পানাগড় টাউন। এই পথে কিছুদূর গাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখলাম, রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে। সাইকেল বা বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে , তবে গাড়ি নিয়ে যাওয়া মুশকিল। অগত্যা ফিরে আসতে হলো। তবে রাস্তার ধারে দেখা মিললো বোদাই নদীর। নদীবুকে ভাসমান কচুরিপানা। নদী আজ শীর্ণকায় , সভ্যতার চাপে আজ খালে রূপান্তরিত। শুধু বোদাই নয়, একই অবস্থা আজ বাংলার অন্যান্য নদীরও ।
ফিরে এলাম সেই ব্রহ্মাণী মন্দিরের কাছে , কোনো ঝুঁকি না নিয়েই যে পথে এসেছিলাম , সেই পথেই ফিরে চললাম। ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো। এদিকে সবারই প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। সড়কের ধারে এক ভাতের হোটেল পেলাম , হোটেল চালান এক বয়স্ক মহিলা এবং তাঁর ছেলে। ওনারাই জানালেন শুধুমাত্র ডিম্ ভাত রয়েছে। তাই অর্ডার দিয়ে মহিলার ছেলের সাথে গল্প করতে লাগলাম। কোথা থেকে এসেছি জানালাম , কি করতে এসেছিলাম জানাতে , উনি আমাদের এক জঙ্গলের সন্ধান দিলেন। খাওয়াদাওয়া সেরে , কৌতূহলী হয়ে ওনার কাছে পথনির্দেশ চাইলাম। ওনার কাছেও জানতে চাইলাম জঙ্গল পাঁচমাথার নাম শুনেছেন নাকি , উনি বললেন – এতদিন এখানে ব্যবসা করছি , এরম জায়গার নাম শুনিনি।

আমি ম্যাপে যে ছবিটা দেখেছিলাম সেটা একজনের আপলোড করা , একজনের রিভিউ দেয়া জায়গা। তাই বিশেষ সহযোগিতা আশা করা যায়না। হয়তো ভুল পয়েন্ট করা থাকতে পারে। তাই আশা ছাড়লাম। জঙ্গল পাঁচমাথা থেকে পাঁচমাথা কে বাদ দিয়ে শুধু জঙ্গলের খোঁজে চললাম।
জায়গাটির নাম বীরসিং এর জঙ্গল। ভদ্রলোক জানালেন , জাতীয় সড়ক থেকে বর্ধমানের দিকে যেতে , রাস্তার ডানদিকের রাঙামাটির রাস্তা ধরতে , সে রাস্তাই আবার গোল হয়ে ঘুরে জাতীয় সড়কেই উঠবে। কিন্তু আমাদের জঙ্গল ঘোরা হয়ে যাবে। সবাই মিলে সাহস করে এগিয়ে গেলাম। ওই যে প্রথমেই বললাম , আমরা চারজন একসাথে বেরোলেই একটা সাংঘাতিক কিছু হওয়ার আশঙ্কা থাকে , সেই ভয়টাই এবারও হচ্ছিলো। তবে আমার নয় , আমার সহযাত্রীদের। ভরসা বলতে সেই বুম্বার ফোন। এতক্ষন উনি রেস্টে ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিলো রাস্তা হারিয়ে গেলেও, আমি কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবো। ব্যাক আপ এর জন্যে সবাই নিজের নিজের ফোনে গুগল ম্যাপ অন করলাম।
গাড়ি রাঙামাটির পথ ধরলো বটে , তবে এতটা চড়াই , উৎরাই আমরা কেউই আশা করিনি। রাস্তাজুড়ে শুধুই লাল ধুলো। ধীরে ধীরে আমরা এক আদিবাসী গ্রামে এসে পড়লাম। গ্রামের ঘরবাড়ি সেটাই জানান দিতে লাগলো। আমাদের মাথায় ছিল , রাস্তা গোল হয়ে ঘুরবে। তাই টার্নগুলোতে আমাদের ডানদিকে যেতে হবে। কিন্তু সববারের মতোই এবারেও থিওরি কিছুক্ষনের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হলো। অনেক জায়গায় দেখতে পেলাম ডানদিকে যাওয়ার রাস্তা নেই , বা খারাপ রাস্তা। অগত্যা বামদিকে যেতে হলো। জানিয়ে রাখি , আমাদের কারো ফোনেই টাওয়ার নেই। শুধুমাত্র বুম্বার ফোন ম্যাপ দেখিয়ে চলেছে। সেদিকে পাত্তা না দিয়ে আমি রাস্তা ঠাহর করতে লাগলাম। বুঝলাম বৃত্তের পরিধি বেড়ে গেছে। আমরা জঙ্গল কিছুই পাইনি , শুধু গ্রামের ভেতর দিয়েই চলেছি। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি , তারা জাতীয় সড়কের কথা শুনতেই সোনামুখীর রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষন এভাবে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘোরার পর, একসময় আমি বললাম , বুম্বা গাড়ি থামা তো। আমি দেখছি। বুম্বা গাড়ি দাঁড় করালো। আমি গাড়ি থেকে নেমে সামনে কয়েকটি বাড়ি দেখতে পেলাম। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম গ্রামের এক অল্পবয়সী গৃহবধূ মাথায় কাঠের বোঝা চাপিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আমি দৌড়ে গেলাম। একবার মনে হলো আমার ভাষা কি যিনি বুঝবেন , বা উনি কি বলবেন সেটা কি আমি বুঝতে পারবো ! পরোয়া না করেই বললাম – দিদি , আমরা অনেক ক্ষণ থেকেই ঘুরে যাচ্ছি , জঙ্গল পাচ্ছি না। বীরসিংয়ের জঙ্গলটা কোথায় বলতে পারেন ?
গৃহবধূ ঈষৎ হেসে সামনে ইশারা করে বললেন – ” ই তো সামনেই গো ! “

আমি ওদিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারলাম না। গ্রামের যেমন রাস্তা হয় ঠিক সেরম লাগলো। গৃহবধূর ওপর ভরসা করে বুম্বাকে বললাম , গাড়ি নিয়ে এগোতে। গাড়ি নিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এগোতেই দেখলাম গ্রামীণ রাঙামাটির রাস্তা ছেড়ে আমরা ঝকঝকে পিচের রাস্তায় উঠতে পড়েছি। বুঝলাম , বীরসিং এর জঙ্গল এসে গেছে। পথের দুধারে ঘন শালবন। এপ্রিল মাসের নতুন পাতা গজানো গাছের সবুজ রং, মাঝের কালো সড়ক আর চারিদিক নিস্তব্ধ। এরম পরিবেশ কি আর বারবার পাওয়া যায় ! গাড়ি থেকে নেমে অনেকগুলো ছবি তুললাম। এতক্ষনে আমার বন্ধু সুব্রত বললো – আকাশের দিকে দেখ ! আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিক ধীরে ধীরে কালো হয়ে আসছে। বুঝলাম বৃষ্টি এলো বলে। তাড়াতাড়ি সব্বাই গাড়িতে এসে বসলাম। বুম্বা গাড়ি নিয়ে একটু এগোতেই দেখতে পেলাম , রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। বামদিকের রাস্তা ঝকঝকে , ডানদিকের রাস্তা ভাঙাচোরা। বুম্বার ফোন দেখাচ্ছে ডানদিকে। বললাম ফোনের ওপর ভরসা করলে হবে না , আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ম্যাপে কি দেখাচ্ছে ? টাওয়ার নেই , উত্তর এলো। এমন সময় দেখি , একজন লোক সাইকেল নিয়ে আসছে। গাড়ি থেকে হাত দেখিয়ে ওনাকে থামতে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম , দাদা বর্ধমানের দিকে যাবো। সড়ক কোনপথে পড়বে ? ভদ্রলোক ওই ঝকঝকে রাস্তার দিকে ইশারা করে বললেন , এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান সোনামুখী। ওখান থেকে বর্ধমানের সড়ক পেয়ে যাবেন।
আমি বুম্বাকে বললাম , হোটেলের ভদ্রলোক এতটা ঘোরার কথা তো বলেননি ? তাহলে উপায় ?
একটাই উপায় – বুম্বার ফোনকে বিশ্বাস করে ডানদিকে যাওয়া। সব্বাই একমত হলো। চললাম ডানদিকে।
দুমিনিট হয়েছে কি , প্রচন্ড বৃষ্টি নামলো। চারিদিক অন্ধকার। গভীর জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে , আশেপাশে কোনো জনপ্রাণীর দেখা নেই। হোটেলের ভদ্রলোক বলেছিলেন , এইপথে হাতির ভয় আছে। এতকিছু ভাবছি , আর এদিকে খারাপ রাস্তা দিয়ে গাড়ি হেলতেদুলতে এগিয়ে চললো। কয়েক কিলোমিটার এভাবেই চলার পর রাস্তার বামদিকে ফরেস্ট অফিস দেখতে পেলাম। ঘন জঙ্গলের ভেতরে ভুতুড়ে বাড়ির মতো একটি একতলা কটেজ। বাড়ির রং সাদা। বাড়ির সামনের বারান্দায় দেখলাম এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ির দিকেই তাকিয়ে আছেন। বৃষ্টির তীব্রতা তখন একটু কমেছিল, সামনে থেকে এক মোটর আরোহীকে আসতে দেখলাম। বাইক রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ফরেস্ট অফিসের দিকে ছুটে গেলো। আমরাও গাড়ি দাঁড় করালাম। লক্ষ্য করলাম ফরেস্ট অফিসের পাশে একটা ওয়াচ টাওয়ার ও রয়েছে।

এতক্ষন রাস্তার শুধু বামদিক দেখছিলাম। ডানদিকে চোখ পড়তেই , আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলাম। বৃষ্টি তখনও থামেনি , গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ছুটে গেলাম। আবিষ্কারের আনন্দ ঠিক যেমন হয় , আমার মনের অবস্থাও তখন সেইরকম। ডানদিকে যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি , সেটি একটি মোড় , পাঁচমাথার মোড়। যেদিক থেকে এলাম আর যেদিকে যাচ্ছি ঐদুটি বাদ দিলে জঙ্গলের ভেতর ৩টি রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা তিনটি কাঁচা লালমাটির। ছবি তুললাম। তারপর গাড়িতে এসে বসলাম। স্ত্রী বলে উঠলো – কি পাগলামি করো ? অন্ধকার হয়ে এসেছে , তার মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছ ? বাড়ির দিকে চলো এবার, অনেক হয়েছে । অগত্যা নিজের আনন্দ নিজের মনেই চেপে রেখে রওনা দিলাম।

কিছুদূর এগিয়ে দামোদর ক্যানাল পেরিয়ে সড়ক পথে এসে পড়লাম। ধন্য বুম্বার ফোন , সঠিক সময়ে সঠিক পথ দেখাবার জন্য। সড়কপথে এসে যেন ফোনও একটু মৃদু হাসি দিলো , তারপর বন্ধ। বুম্বা বললো – এমা , ব্যাটারি শেষ। চার্জে বসাতে হবে। সুব্রত বললো – আর চিন্তা নেই , সোজা গেলেই বর্ধমান , তারপর ডানদিকের সড়ক ধরলেই বাড়ি পৌঁছে যাবো।
বাংলার গ্রামে ঘোরার যে বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলি আমার হয়েছে, তার মধ্যে এটিও যোগ হলো। বীরসিং এর জঙ্গল , সেই আদিবাসী গৃহবধূ , জমিদারবাড়ির মন্ডলবাবু ,কাউকেই আমি ভুলতে পারবো না। ভুলতে পারবো না , মানুষের প্রতি মানুষের আন্তরিকতা। আমাদের মধ্যে যতই বৈষম্য থাকুক না কেন , আন্তরিকতা যেন ওনাদের সহজাত অধিকার। জানিয়ে রাখি , জমিদারবাড়ির মন্ডলবাবুর কথা যে বলেছিলাম , উনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওনার বাড়িতে এসে মধ্যাহ্নভোজ করার। যদিও এতজন মিলে যাওয়াটা ঠিক দেখায় না , তাই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তবুও ওনার এই আন্তরিকতা আমি ভুলিনি। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা মানুষকে আপন করে নেয়ার। দুর্গাপুজোয় নিমন্ত্রণ করলেন। সপরিবারে আসতে বলেছিলেন।
এই ব্যবহার আমি বাংলায় বারবার খুঁজে পেয়েছি। সে চুপি গ্রাম হোক, বা মেদিনীপুর কিংবা বৈদ্যপুর , সর্বত্রই মানুষের এই আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কখনো টোটোচালক , কখন মন্ডলবাবুর মতো জমিদার পরিবারের সদস্য , আন্তরিকতা জাতি, ধর্ম, পেশা নির্বিশেষে আমি পেয়েছি। তাই তো পেশাগত কারণে বাংলা ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও , কখনই যেতে পারিনি , জানিনা ভবিষ্যতেও পারবো কিনা !